বাংলাদেশ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রযুক্তিনির্ভর রূপান্তরের পথে এগোচ্ছে। মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইন শিক্ষা, টেলিমেডিসিন, ই–কমার্স কিংবা তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর প্রশাসন—প্রতিটি খাতেই ইন্টারনেট অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভিডিও স্ট্রিমিং, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, অনলাইন গেমিং ও ক্লাউডভিত্তিক সেবা। অর্থনীতি, শিক্ষা ও প্রশাসনের এই নির্ভরতার কেন্দ্রে রয়েছে ইন্টারনেট অবকাঠামো।
কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—এই অবকাঠামো কতটা টেকসই? সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনা আমাদের দেখিয়েছে, সামান্য একটি দুর্ঘটনাই জাতীয় পর্যায়ে বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে। ফলে আজকের বড় প্রশ্ন, আমরা কি সত্যিই একটি স্থিতিশীল ও টেকসই ইন্টারনেট ব্যবস্থার দিকে এগোচ্ছি?
ইন্টারনেট গ্রাহক কত?
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সূত্র মতে দেশের মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৫১ লাখ ৫৮ হাজার ৬১৬ জন। অন্যদিকে, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে দেশের মোট ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১৩ কোটি ১০ লাখ। এর মধ্যে প্রায় ১১ কোটি ৮৪ লাখ ৯০ হাজার জন মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারী এবং প্রায় ১ কোটি ২৮ লাখ ৮০ হাজার জন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবহারকারী।
মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের বিস্তার
বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) খাত দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। বর্তমানে গ্রাহক ও মার্চেন্ট মিলিয়ে এমএফএস হিসাবের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৪ কোটি ০৪ লাখ ৬৬ হাজার ৩৩৪টি, যার মধ্যে সক্রিয় হিসাবের সংখ্যা প্রায় ৮ কোটি ৭১ লাখ ৫৪ হাজার। এই খাতে প্রতিমাসে মোট লেনদেনের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১,৬৪,৭২৬ কোটি টাকা, অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৫,৮৮৩ কোটি টাকার আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন হচ্ছে।
সরকারি ইউটিলিটি বিল অনলাইনে পরিশোধ
বাংলাদেশে ইন্টারনেট ও মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে বিভিন্ন সরকারি ইউটিলিটি বিল অনলাইনে পরিশোধ করা যায়। এর মধ্যে প্রধানত বিদ্যুৎ বিল (যেমন পিডিপিসি, টিটাস, রূপালি বিদ্যুৎ), পানি বিল (ঢাকা ওয়াসা, চট্টগ্রাম ওয়াসা, অন্যান্য স্থানীয় পানি সরবরাহ সংস্থা), গ্যাস বিল (বিপিজিসিএল), কর ও ভ্যাট সংক্রান্ত বিল, এবং পৌরসভার পরিষেবা ফি ও ট্রেড লাইসেন্স অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া কিছু এলাকায় ট্রাফিক জরিমানা ও অন্যান্য প্রশাসনিক ফিও অনলাইনে পরিশোধ করা যায়। এই সেবাগুলো ব্যাংকিং সিস্টেম, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস এবং সরকারি ওয়েবপোর্টালের মাধ্যমে সহজে পাওয়া যায়।
সাবমেরিন কেবল: সীমিত বৈচিত্র্যের ঝুঁকি
বাংলাদেশ বৈদেশিক ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের জন্য প্রধানত দুটি সাবমেরিন ক্যাবল—SEA-ME-WE-4 ও SEA-ME-WE-5—এর ওপর নির্ভরশীল। এই সীমিত নির্ভরতা একাধিকবার জাতীয় সেবাকে হুমকির মুখে ফেলেছে।
* ২০২০ সালের আগস্টে, পটুয়াখালী এলাকায় নির্মাণকাজ চলাকালে SEA-ME-WE-5 ক্যাবল কেটে যায়। এর ফলে সারাদেশে ইন্টারনেট গতি নাটকীয়ভাবে ধীর হয়ে পড়ে।
* ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে, সিঙ্গাপুর–মালয়েশিয়া অংশে একই ক্যাবলের ত্রুটি দেখা দেয়। কুয়াকাটা–সিঙ্গাপুর রুট বন্ধ হয়ে যায় এবং সেবা স্বাভাবিক হতে প্রায় দুই মাস সময় লেগে যায়।
সিমিউই৪ ক্যাবলটি ২০০৫ সালে পরিষেবা শুরু করে। সাধারণভাবে সাবমেরিন ক্যাবলগুলোর প্রকৌশলগত অথবা আইনি মেয়াদ প্রায় ২৫ বছর ধরা হয়। সিমিউই৪ ক্যাবলটি ২০ বছরের বেশি সময় ব্যবহৃত হচ্ছে। সিমিউই৫ ক্যাবলটির সক্ষমতা কারিগরি ক্রটির জন্য ইতিমধ্যে ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। সিমিউই৬ ক্যাবলটির সাথে বাংলাদেশের সংযুক্ত হওয়ার কথা ছিল ২০২৫ সালে সেটি নিয়েও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।
এই অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে, ক্যাবল কাটা বা আন্তর্জাতিক ত্রুটি ঘটলেই পুরো দেশের তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক জীবন অচল হয়ে যেতে পারে। নতুন রুট ও বিকল্প সংযোগ ছাড়া এই দুর্বলতা কাটানো সম্ভব নয়।
খাজা টাওয়ার অগ্নিকাণ্ড: কেন্দ্রীভূত অবকাঠামোর দুর্বলতা
২০২৩ সালের ২৬ অক্টোবর ঢাকার মহাখালীতে খাজা টাওয়ারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। এতে কয়েকটি ডাটা সেন্টার, আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট গেটওয়ে (IIG) ও ইন্টারকানেকশন এক্সচেঞ্জ (ICX) বন্ধ হয়ে যায়। সারা দেশে ব্রডব্যান্ড ও মোবাইল ডেটা সেবা ব্যাহত হয়। একই বছরের ডিসেম্বরে আবারও একই ভবনে অগ্নিকাণ্ড ঘটে।
এই ঘটনাগুলো প্রমাণ করেছে, জাতীয় পর্যায়ের অবকাঠামো একক স্থানে কেন্দ্রীভূত থাকলে সিঙ্গেল পয়েন্ট অব ফেইলিওর তৈরি হয়। একটি ভবনের ক্ষতি গোটা দেশের সেবা অচল করে দিতে পারে। তাই অবকাঠামোকে ভৌগোলিকভাবে বিতরণ করা ছাড়া বিকল্প নেই।
স্থানীয় কনটেন্ট নোড নেই: ধীরগতি, বাড়তি ব্যয় ও নিরাপত্তা ঝুঁকি
বাংলাদেশে এখনও পর্যন্ত গুগল, ফেসবুক, ইউটিউব, নেটফ্লিক্স বা ক্লাউডফ্লেয়ারসহ আন্তর্জাতিক কনটেন্ট প্রদানকারীরা স্থানীয় নোড বা CDN সার্ভার স্থাপন করেনি। এর ফলে ব্যবহারকারীর ডেটা প্রায়শই বিদেশি সার্ভারের মাধ্যমে ঘুরে আসে, যা ব্যান্ডউইথের অতিরিক্ত খরচ বাড়ায়, সেবার গতি ধীর করে এবং জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি তৈরি করে। প্রতিবেশী দেশ ভারত ও পাকিস্তান ইতিমধ্যেই স্থানীয় কনটেন্ট নোড স্থাপন করে নিজেদের তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামোকে আরও শক্তিশালী ও স্বনির্ভর করেছে। তারা ব্যান্ডউইথ সাশ্রয় করছে, দ্রুততর সেবা পাচ্ছে এবং কৌশলগতভাবে স্বনির্ভরতা বাড়িয়েছে। বাংলাদেশ এখনও সেই অবস্থানে পৌঁছাতে পারেনি।
জাতীয় নিরাপত্তা স্বার্থে নিক্স শক্তিশালীকরণ
বাংলাদেশে ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ (NIX) বিদ্যমান থাকলেও এর কার্যকারিতা সীমিত। দেশের ভেতরের ট্রাফিকও অনেক সময় বিদেশি রুট ঘুরে আসে, যার ফলে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বেড়ে যায়, সাইবার নিরাপত্তার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় এবং অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ অকার্যকর হয়ে পড়ে। যদি শক্তিশালী নিক্স বাস্তবায়ন করা হয় এবং বাধ্যতামূলক স্থানীয় পিয়ারিং চালু করা যায়, তবে দেশীয় ডেটা দেশেই থাকবে। এতে খরচ কমবে, সাইবার নিরাপত্তা বাড়বে এবং জরুরি পরিস্থিতিতে জাতীয় নিরাপত্তা স্বার্থে অভ্যন্তরীণ ইন্টারনেট সংযোগ সচল রাখা সম্ভব হবে।
উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশে ইন্টারনেট শাটডাউন হওয়ায় সরকারি ইউটিলিটি বিল অনলাইনে পরিশোধ স্থগিত হয়। অনলাইন পেমেন্ট ব্যবস্থা বৈদেশিক ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়ায় এই সময়ে লেনদেন বন্ধ হয়ে যায়। জাতীয় অবকাঠামো বা নিক্স শক্তিশালী হলে স্থানীয় ট্রাফিক দেশেই পরিচালিত হতে পারতো, ফলে অভ্যন্তরীণ পরিষেবা ও বিল পরিশোধ অব্যাহত রাখা সম্ভব হতো।
.bd ডোমেইন এবং নিরাপত্তা তুলনা
.bd হল বাংলাদেশের কান্ট্রি-কোড টপ-লেভেল ডোমেইন (ccTLD), যা বিটিসিএল দ্বারা পরিচালিত। ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান .com.bd, .org.bd, .net.bd-এর মতো সাবডোমেনের মাধ্যমে নিবন্ধন করতে পারে, আর .gov.bd শুধুমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য সংরক্ষিত। স্থানীয় সার্ভার ও ট্রাফিকের কারণে .bd তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ও কম ঝুঁকিপূর্ণ। বিপরীতে .com, .org, .net, .gov বিশ্বব্যাপী সার্ভার ও DNS-নির্ভর, যা সাইবার হামলা বা সার্ভার সমস্যায় বেশি প্রভাবিত হতে পারে। তাই বাংলাদেশের জন্য শুধুমাত্র .bd ব্যবহার নিরাপদ। ভূরাজনীতি ও জাতীয় স্বার্থের কারণে বাংলাদেশে সাবডোমেন ব্যবহার না করাই ভালো, অন্যান্য দেশ তাই করছে। সাবডোমেন ব্যবহারের জন্য অযথা বৈদেশিক মুদ্রাও ব্যয় হচ্ছে। গত পাঁচ বছরে .bd ডাউনটাইম হয়েছে, যেমন ডিসেম্বর ২০২০-এ পাওয়ার সমস্যা ও এপ্রিল ২০২৪-এ প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে কিছু ওয়েবসাইট ডাউন হয়েছিল।
নিরাপত্তা ও রেগুলেটরি ঘাটতি
বাংলাদেশের অনেক ডাটা সেন্টার এখনও আন্তর্জাতিক মানের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, ব্যাকআপ বিদ্যুৎ কিংবা দুর্যোগ পুনরুদ্ধার প্ল্যান ছাড়া চলছে। নিয়মিত রেগুলেটরি অডিটের অভাবও স্পষ্ট। এর ফলে অবকাঠামোর নিরাপত্তা দুর্বল থেকে যাচ্ছে এবং হঠাৎ কোনো বিপর্যয়ে জাতীয় সেবা থমকে যাওয়ার ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে।
টেকসই ইন্টারনেট নিশ্চিতের করণীয়
বাংলাদেশের ইন্টারনেট অবকাঠামো টেকসই করতে এখনই কিছু পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। সেগুলো হলো—
১. নতুন সাবমেরিন ক্যাবলে রুট, স্যাটেলাইট এবং টেরেস্ট্রিয়াল সংযোগ তৈরি — আন্তর্জাতিক বৈচিত্র্য বাড়াতে হবে।
২. ভৌগোলিকভাবে বিতরণকৃত ডাটা সেন্টার ও আইআইজি — কেন্দ্রীভূত অবকাঠামো থেকে বের হতে হবে।
৩. স্থানীয় কনটেন্ট নোড ও সিডিএন সার্ভার স্থাপন — আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলোকে উৎসাহিত করতে হবে।
৪. আধুনিক ফায়ার-সেফটি ও রেগুলেটরি অডিট — নিয়মিত মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে হবে।
৫. জাতীয় দুর্যোগ পুনরুদ্ধার প্ল্যান তৈরি — দুর্যোগে বিকল্প সেবা চালু রাখা অপরিহার্য।
৬. জাতীয় স্বার্থে .bd ডোমেইন — নিরাপত্তা এবং বৈদেশিক মুদ্রা বাচাতে সাবডোমেন ব্যবহার করা যাবে না।
৭. শক্তিশালী নিক্স ও বাধ্যতামূলক দেশীয় পিয়ারিং — দেশীয় ট্রাফিক দেশেই রাখতে হবে।
নতুন টেলিকম নীতি: সুযোগ ও সংশয়
বাংলাদেশের নতুন টেলিকম নীতিতে কিছু ইতিবাচক দিক রয়েছে। এর মধ্যে ৫জি চালুর পরিকল্পনা, স্যাটেলাইট সেবা ব্যবহার, আন্তর্জাতিক গেটওয়ে আধুনিকায়ন এবং গ্রামীণ সংযোগ সম্প্রসারণ অন্তর্ভুক্ত। এই পদক্ষেপগুলো প্রযুক্তিনির্ভর রূপান্তরের জন্য সুযোগ তৈরি করেছে এবং দেশের ইন্টারনেট অবকাঠামো আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
তবে সমালোচকদের মতে, নীতিতে বেসরকারি খাত ও প্রযুক্তি অংশীজনদের সক্রিয় অংশগ্রহণের অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় ঘাটতি হলো স্থানীয় কনটেন্ট নোড স্থাপন, শক্তিশালী NIX গড়ে তোলা এবং দুর্যোগ পরিস্থিতিতে ইন্টারনেট স্থিতিশীল রাখার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনার অনুপস্থিতি। এছাড়া স্পেকট্রাম নিলামের মূল্য, কর–জটিলতা এবং অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ বিনিয়োগের পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে।
ফলে প্রশ্ন থেকে যায়—এই নীতি দীর্ঘমেয়াদে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারবে কি না, নাকি বিদ্যমান সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলবে? এর উত্তর নির্ভর করবে নীতির বাস্তবায়নের স্বচ্ছতা এবং বহুপক্ষীয় অংশগ্রহণের ওপর।
উপসংহার
বাংলাদেশের প্রযুক্তিনির্ভর রূপান্তর এগুচ্ছে, কিন্তু এর মূলভিত্তি—ইন্টারনেট অবকাঠামো—এখনও ভঙ্গুর। সাবমেরিন ক্যাবলের সীমিততা, কেন্দ্রীভূত ডাটা সেন্টার, স্থানীয় কনটেন্ট নোডের অভাব এবং দুর্বল নিক্স দেশের ডিজিটাল সেবাকে ঝুঁকিপূর্ণ করছে। এই পরিস্থিতি অনলাইন শিক্ষা, মোবাইল ব্যাংকিং, টেলিমেডিসিন ও সরকারি ইউটিলিটি বিল পরিশোধসহ দৈনন্দিন কার্যক্রমকে প্রভাবিত করতে পারে। সরকারের নীতি যদি স্থানীয় কনটেন্ট নোড স্থাপন, শক্তিশালী নিক্স, বিকল্প রুট ও দুর্যোগ পুনরুদ্ধার প্ল্যান বাস্তবায়ন করে এবং বেসরকারি খাত ও প্রযুক্তি অংশীজনদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে, তাহলে বাংলাদেশ একটি স্থিতিশীল, নিরাপদ ও টেকসই ইন্টারনেট ব্যবস্থার দিকে এগোতে পারবে। স্বচ্ছ বাস্তবায়ন, নিয়মিত তদারকি এবং বহুপক্ষীয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা না হলে প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়ন সবসময় ঝুঁকির মধ্যে থাকবে।
মোহাম্মদ আব্দুল হক অনু
মহাসচিব, বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স ফোরাম এবং ফেলো, আইসক কমিউনিটি ২০২৫

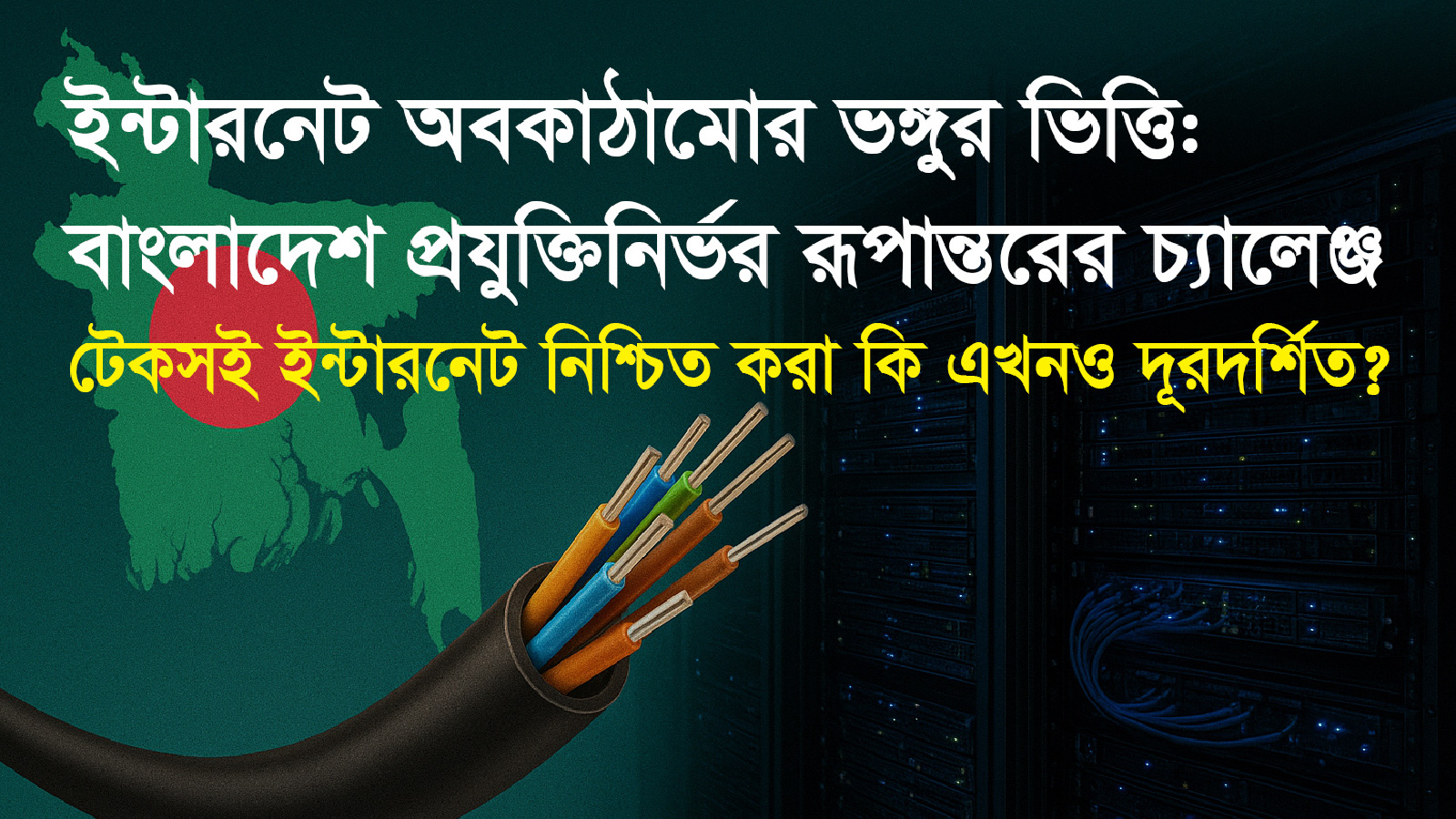




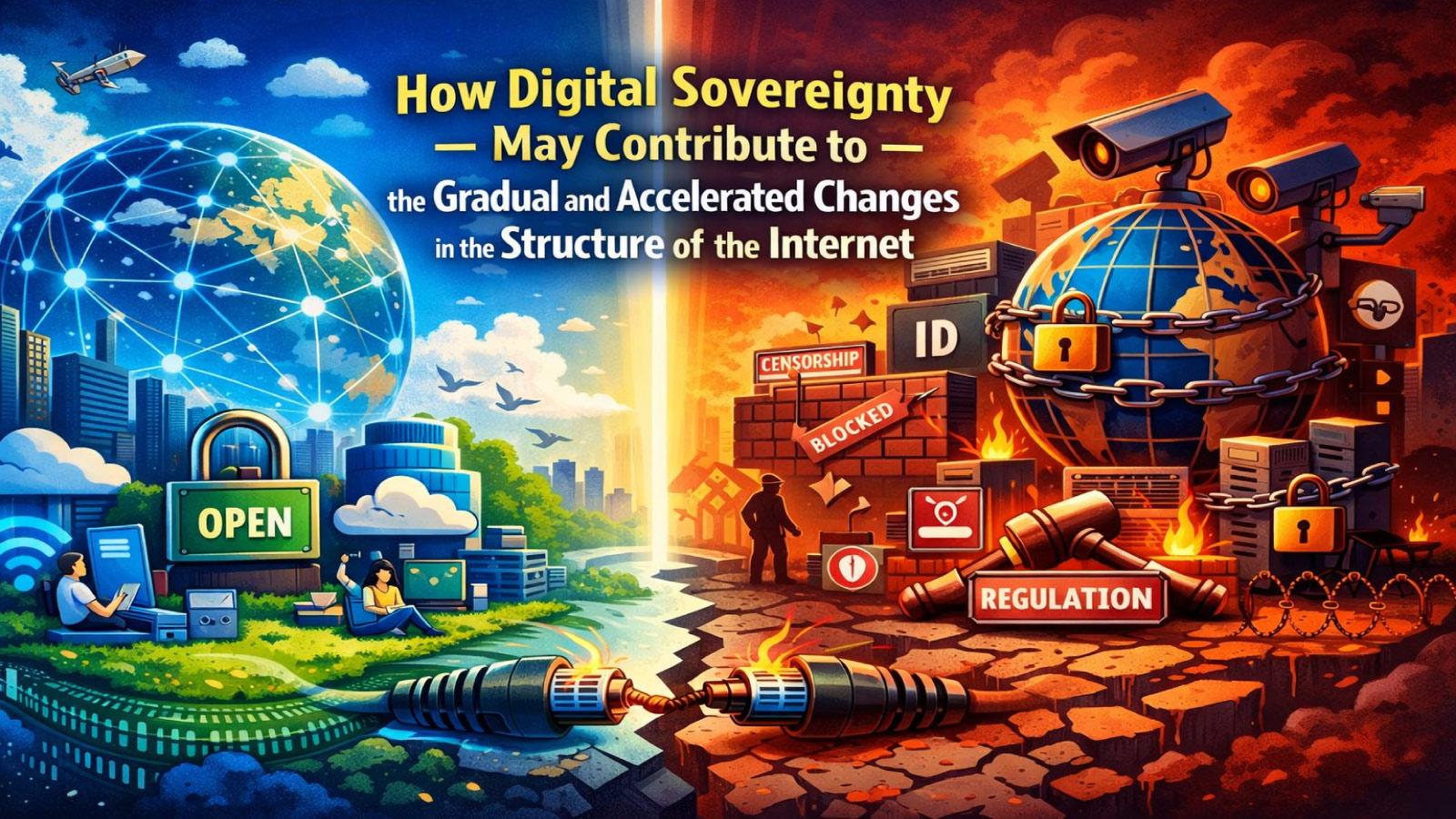

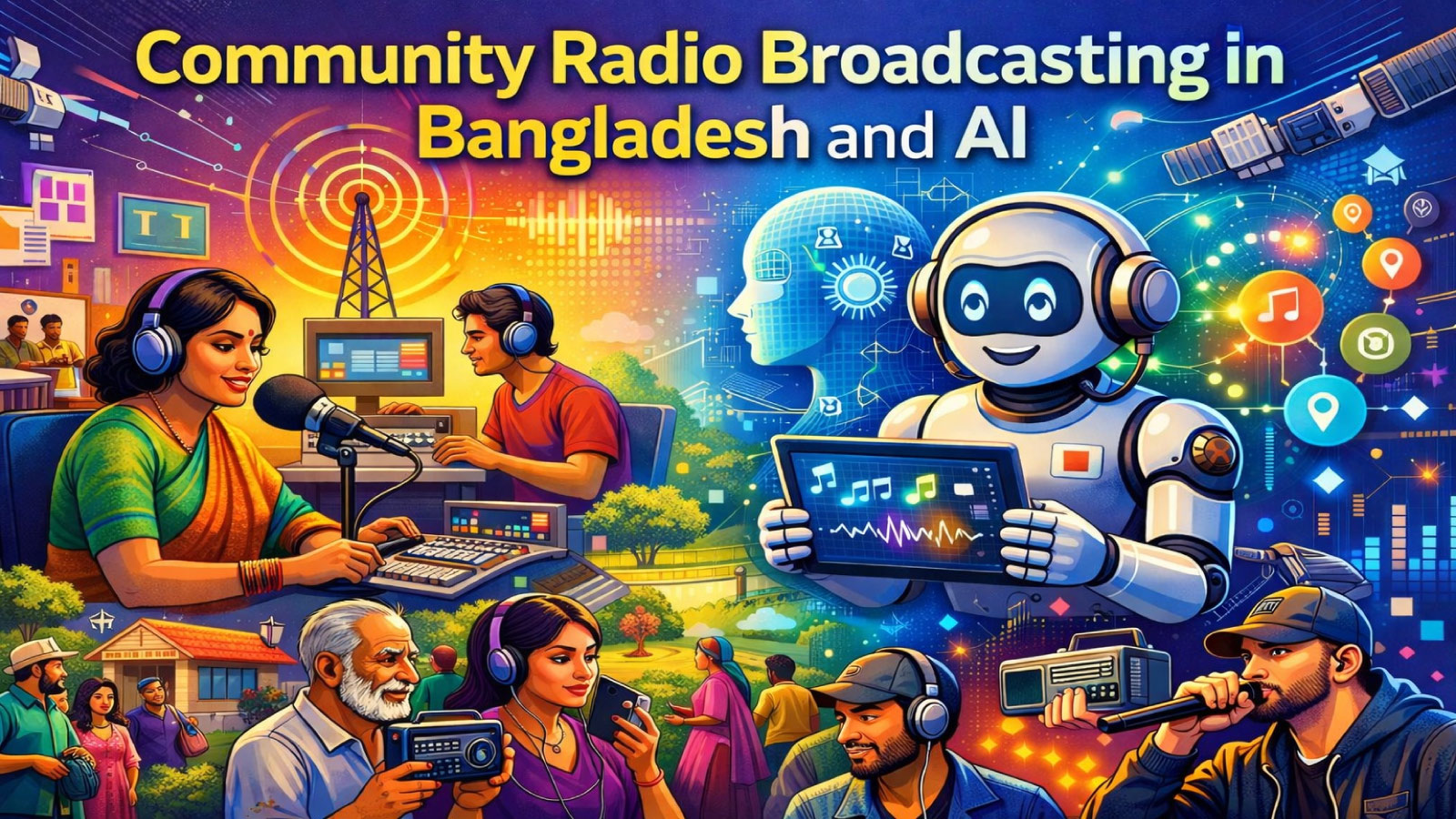
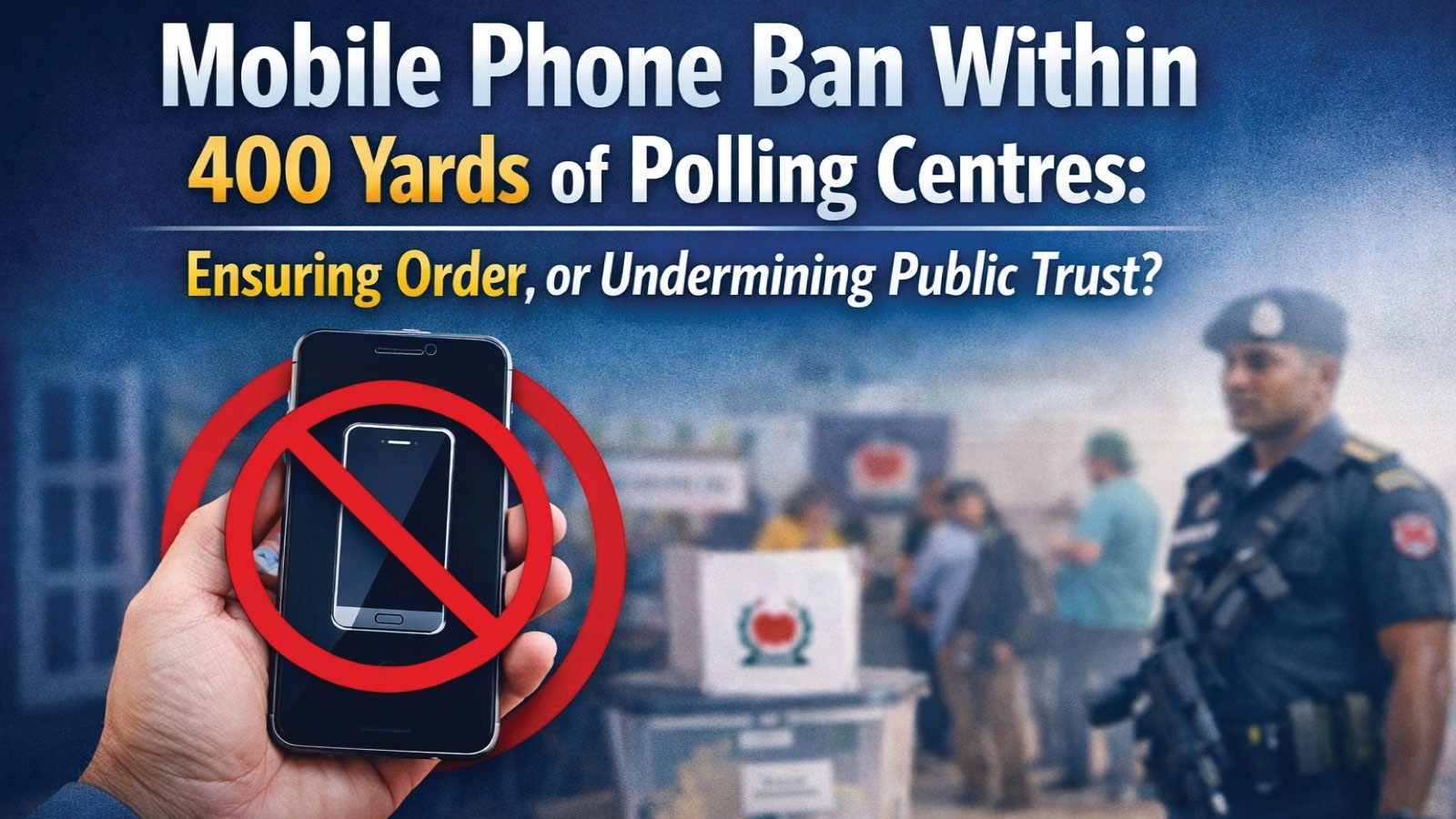




০ টি মন্তব্য